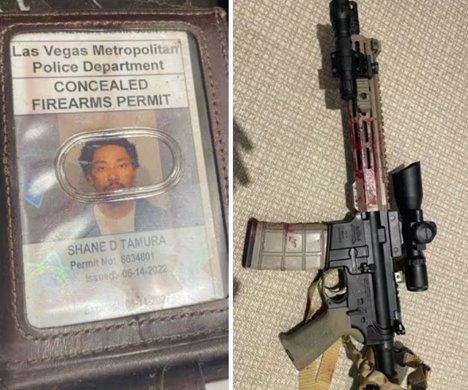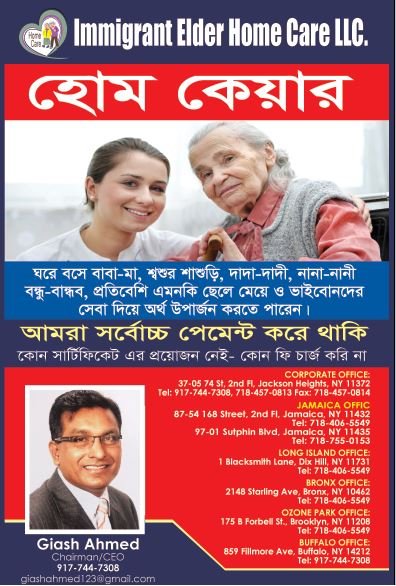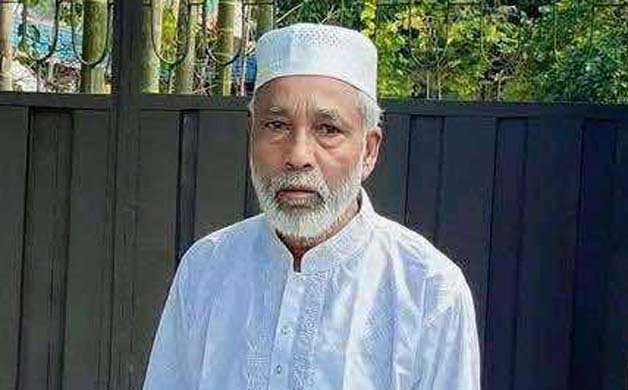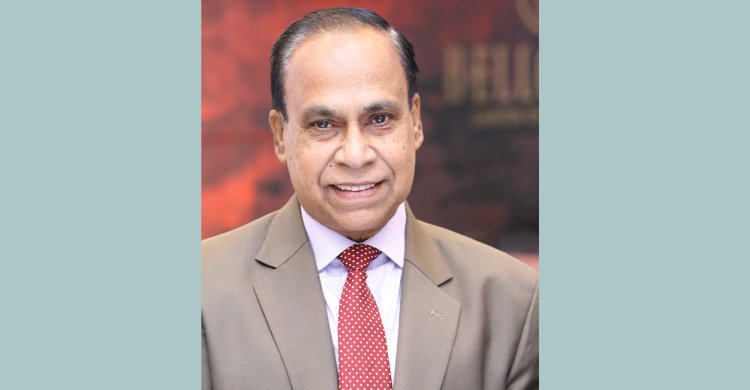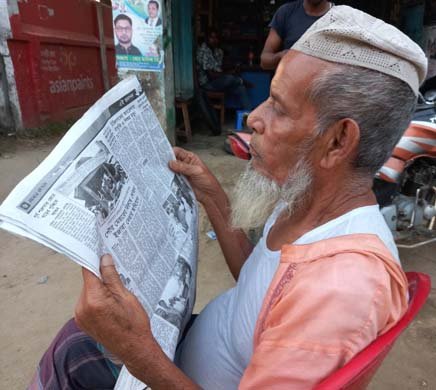যে কারণে মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ

- প্রকাশের সময় : ০৮:৪৭:৪২ অপরাহ্ন, বৃহস্পতিবার, ৮ নভেম্বর ২০১৮
- / ৬৮৩ বার পঠিত
অ্যান্ড্রু হ্যামন্ড: যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে আভাস পাওয়া গেছে, অনেক ভোটার এ নির্বাচনের ব্যাপারে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উৎসাহী এবং কিছু রাজ্যে দেখা যাচ্ছে ভোট পড়ার হার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মতোই। কেবল যুক্তরাষ্ট্রের জনগণই যে এ নির্বাচনী প্রচারণা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন, তা কিন্তু নয়। বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা আগ্রহ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছেন ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকানদের মাঝে মূলনীতি সংক্রান্ত পার্থক্যগুলো, সর্বোপরি কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ আঁকড়ে ধরে বড় আকারে ছড়ি ঘোরানোর বিষয় বিবেচনায় নিয়ে।
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের বৈশ্বিক আবেদনের একটি কারণ হল মধ্যবর্তী নির্বাচনকে দেখা হচ্ছে ট্রাম্পের দুই বছরের প্রেসিডেন্ট মেয়াদের গণভোট হিসেবে এবং এ কারণে নির্বাচনের ফলাফল আগাম সংকেত দেবে ২০২০ সালে প্রেসিডেন্ট পুনর্নিবাচিত হচ্ছেন কিনা। তবে মধ্যবর্তী নির্বাচনটি বিদেশিদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার আরও গভীর কারণ হল নির্বাচনী প্রচারণায় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যু অতি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা।
উদাহরণ হিসেবে কয়েক হাজার মানুষের তথাকথিত ‘শরণার্থী কাফেলা’র বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে, যার যাত্রা হন্ডুরাস থেকে কয়েক সপ্তাহ আগে শুরু হয়েছে এবং যার পেছনের কারণ হিসেবে ট্রাম্প জোর দিয়ে ডেমোক্রেটদের দায়ী করছেন। ওই শরণার্থী কাফেলাটি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্ত থেকে প্রায় এক হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছে।
শরণার্থী ইস্যু বেশিরভাগ সমর্থকের কাছেই মূল আকর্ষণ, বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে নিজের সমর্থকদের উসকে দিতে ট্রাম্প নিরবচ্ছিন্নভাবে বিষয়টি ব্যবহার করেছেন এবং সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে শরণার্থী কাফেলাটির যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ছুটে আসা থামিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
প্রচারণায় সুবিধা নিতে আরেকটি আন্তর্জাতিক ইস্যু ব্যবহার করা হয়েছে, যা হল যুক্তরাষ্ট্র-চীনের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যযুদ্ধ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইঁদুর দৌড়ের বিষয়টি। জনসমক্ষে কোনো ধরনের প্রমাণ দেয়া ছাড়াই গত মাসে ট্রাম্প জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ করেছেন, মধ্যবর্তী নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার জন্য কাজ করছে চীন।
এশিয়ার শক্তিমান দেশটির প্রতি হোয়াইট হাউসের অবস্থানের কারণে চীনের অখুশি মনোভাবের জন্য তেমনটি করা হবে বলে দাবি করেছেন তিনি। এটি জোর দিয়ে বলা হচ্ছে, কারণ ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প জয়ী হয়েছিলেন ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ প্লাটফর্মে থেকে। এখন তিনি কেবল এমন একটি বিষয়েই জড়িত নন, যা চীনের সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, একইসঙ্গে তিনি নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (নাফটা) নিয়ে আবার আলোচনা শুরু করতে সম্প্রতি একমত হয়েছেন।
এশিয়ার মিত্রদের সঙ্গে ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ বাতিল করার পর এ চুক্তিটিকে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকো চুক্তি বলে নতুন নামে ডাকা হচ্ছে।
এ বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনী প্রচারণায় আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলোর প্রাধান্য মূলত ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় থেকে নিয়মিতভাবে আকৃতি পাওয়া শুরু করে এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প জয়ী হন।
ওই বছর পিউ রিসার্চ সেন্টারের গবেষণায় উঠে এসেছিল, জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশই বিশ্বাস করত আমেরিকা যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে তার মধ্যে পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক চ্যালেঞ্জই ছিল সবচেয়ে বড়। এর বিপরীতে ‘মাত্র’ ২৩ শতাংশ আমেরিকান অভ্যন্তরীণ, বিশেষত অর্থনৈতিক সমস্যার কথা উল্লেখ করেছিল।
গত কয়েক দশকের যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাসে অর্থনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ ইস্যুর তুলনায় পররাষ্ট্র বিষয়ক ইস্যুর প্রাধান্য পাওয়ার বিষয়টি নজিরবিহীন। অবশ্য এটা ১৯৪৮ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ¯œায়ুযুদ্ধের প্রথম ২৫ বছরের সঙ্গে অনেক বেশি মিলে যায়। তখন নির্বাচনী প্রচারণার সময় যুক্তরাষ্ট্রের ভোটারদের উদ্বেগকে প্রভাবিত করত আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইস্যুগুলো। এর বিপরীতে, ১৯৭০-এর দশকের শুরু থেকে অর্থনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলি নির্বাচকমন্ডলীর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়ার প্রবণতায় পরিণত হয়। পিউ রির্সাচের তথ্যমতে, ২০১২ সালের র্নিবাচনী বছরের আগে ২০১১ সালে ৫৫ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের সবচেয়ে উদ্বেগের মধ্যে ছিল দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবেলা করার বিষয়টি। বিপরীতে মাত্র ৬ শতাংশ আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতি বা অন্য আন্তর্জাতিক বিষয়কে উল্লেখ করেছিল।
তথাপি, যদিও পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতিগুলো সাময়িকভাবে হলেও ইউএস নির্বাচকমন্ডলী বা ভোটারদের মনের অগ্রভাগে ফিরে এসেছে, তারপরও বর্তমান ও স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ের প্রথম দুই দশকের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। ওই সময়ের শুরুর দিকটা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিল পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে বিস্তৃত আকারে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা এবং ঐকমত্যের ওপর ভিত্তি করে। বিপরীতে, বর্তমানে পররাষ্ট্রনীতি রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি হারে ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকানদের মাঝে সিদ্ধান্তমূলক বিষয় হয়ে পড়েছে।
নিশ্চিতভাবে বলতে গেলে, স্নায়ুযুদ্ধের প্রথম দিককার এ ঐকমত্যের বিষয়টিকে বাড়িয়ে বলা যায়। তা সত্ত্বেও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য একটি মাত্রা পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক মতৈক্য এবং অধিকতর রাজনৈতিক শিষ্টতা বজায় ছিল। এটা ছিল ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকের ভিয়েতনাম যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক টানটান উত্তেজনা এবং চীন-সোভিয়েত বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে একশিলা সমাজতন্ত্রের ভাঙন পর্যন্ত।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্পষ্ট কোনো পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতিবিষয়ক মতৈক্য গড়ে ওঠেনি। উদাহরণস্বরূপ, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি ও অবস্থানকে তারা কীভাবে দেখে- এ প্রশ্নে অনেক রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেট উল্লেখযোগ্যহারে মতানৈক্যের মধ্যে রয়েছে। এছাড়া কোন মাত্রায় দেশটিকে একপাক্ষিক হতে হবে, সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের প্রচারণায় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে ও কোন পদ্ধতিতে এ যুদ্ধ চালানো হবে এবং পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে মূল অগ্রাধিকার কী হবে- এসব বিষয়ে তারা ভিন্নমত পোষণ করে থাকে।
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য বিপর্যয় রোধ যেমন- ওয়ালষ্ট্রিট শেয়ারবাজারে বড় ধরনের ধস, বর্তমানে তুলনামূলক প্রাধান্য পাওয়া পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ইস্যুগুলো বাকি প্রচারণায় মূল প্রভাবক হিসেবে থেকে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। আর এসব বিষয়ে দলকানা বিভক্তি ইউএস ভোটারদের মাঝে উচ্চমাত্রার শক্তিশালী রাজনৈতিক মেরুকরণ হয়ে আভির্ভূত হবে।
সর্বোপরি, প্রচারণার বাকি অংশের জন্য মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে সম্ভবত থেকে যাবে পররাষ্ট্রনীতি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইস্যুগুলো। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দলকানা বিভক্তি পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে আটকে দিয়েছে এবং এসব বিষয়ে রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটদের মধ্যকার দূরত্ব সম্ভবত আরও বাড়তে পারে গুরুত্বপূর্ণ এ মধ্যবর্তী নির্বাচনে, যা ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির ভাগ্য নির্ধারণ করে দিতে পারে।
গালফ নিউজ থেকে অনুবাদ: সাইফুল ইসলাম
অ্যান্ড্রু হ্যামন্ড: লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের এলএসই আইডিয়াস’র সহযোগী (যুগান্তর)