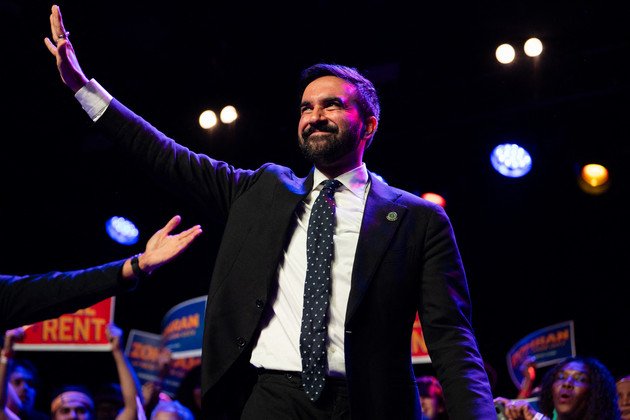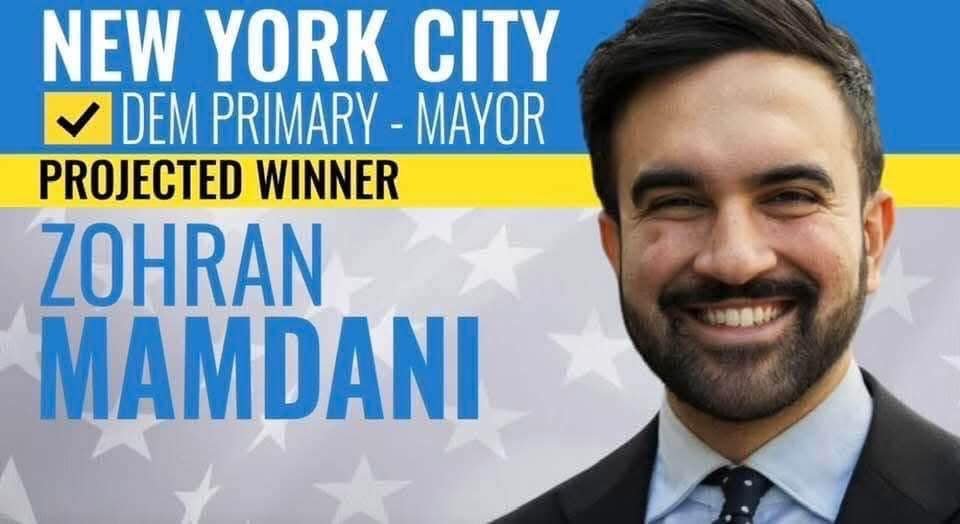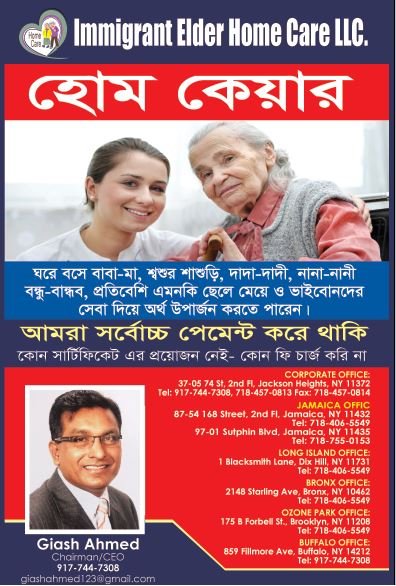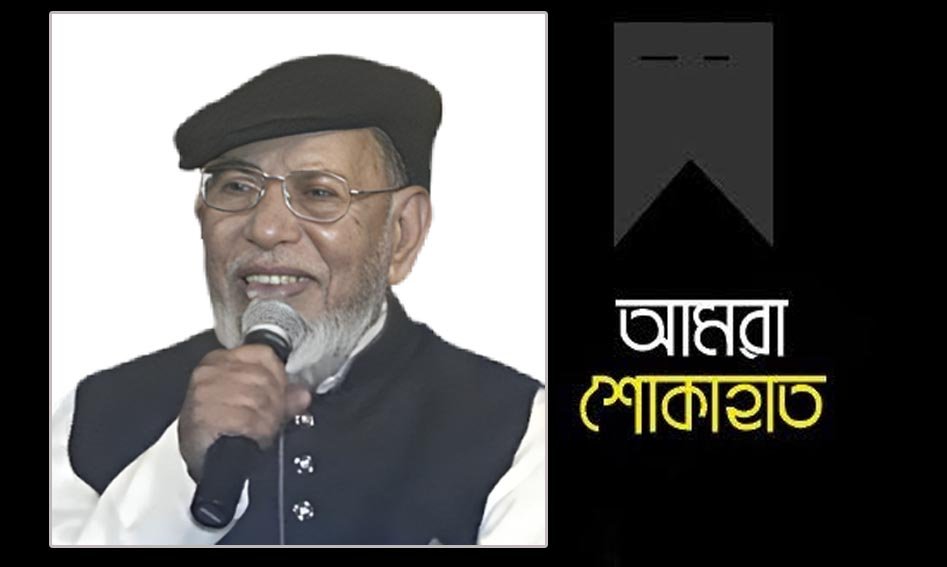প্রভাব রেখেছে যে বিষয়গুলো

- প্রকাশের সময় : ১২:৫৭:১৯ পূর্বাহ্ন, বৃহস্পতিবার, ১৭ নভেম্বর ২০২২
- / ৮৪ বার পঠিত
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ফলাফল এ লেখা তৈরির সময় চূড়ান্ত হয়নি। তবে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি আসনের বিপরীতে রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। বিজয়ী হওয়ার জন্য ২১৮টি সিটে জয়লাভ জরুরি হলেও রিপাবলিকানরা ২২০-২২২টি সিট পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে সিনেটের ১০০টি আসনের মধ্যে উভয়ে ৫০-৫০ আসনে জয়লাভ করবে বলে মনে হচ্ছে। সিনেটের চূড়ান্ত ফলাফল পেতে ডিসেম্বরের ৬ তারিখে জর্জিয়ার রানঅফ ইলেকশন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
এ ফলাফলে ক্ষমতাসীন বাইডেনের ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে। এর ফলে হয়তো কংগ্রেসের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির স্থলাভিষিক্ত হবেন রিপাবলিকানদের নেতা কেভিন ম্যাকারথি। স্পিকার পরিবর্তনের পরপরই সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বর্তমানে চলমান তদন্ত বন্ধ হয়ে উলটো জো বাইডেনের ছেলের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হতে পারে। অবশ্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলে দিয়েছেন, তিনি এসবে ভ্রূক্ষেপ করেন না।
আমেরিকার এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে সবার ধারণা ছিল ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটদের বড় ধরনের পরাজয় হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন রাজ্যে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির কারণে ডেমোক্র্যাটরাও ধরে নিয়েছিল তাদের বড় রকমের পরাজয় হবে। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ায় ডেমোক্র্যাটরা খুশি। অন্যদিকে প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রিপাবলিকানরা খুশি। এ অবস্থায় উভয় দলই উইন-উইন মুডে রয়েছে। কোনো পক্ষেই খুব একটা হতাশা নেই। সবাই অনেকটা খোশ মেজাজে রয়েছে। যার যার ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণে উভয়পক্ষ ব্যস্ত, যাতে ২০২৪-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভালো করা যায়। কোন ইস্যুতে জনগণ কতটা প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, এ বার্তা উভয় দল পেয়ে গেছে। এখন জনগণের দেওয়া সিগন্যাল অনুযায়ী কাজ করতে পারলেই দুবছর পর হোয়াইট হাউজের দখল নেওয়া যাবে-এ বিশ্বাস নিয়েই কাজ করছে দুটি দল।
এবারের নির্বাচনে ভোটারদের মনোজগতে কাজ করেছে প্রধানত দুটি ইস্যু। একটি হচ্ছে আমেরিকায় গত ৪০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূল্যস্ফীতি। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। ভোটারদের দৈনন্দিন ব্যয় বেড়ে গেছে। ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার বাড়িয়েও মূল্যস্ফীতি মোকাবিলা করা যাচ্ছে না। মর্টগেজ রেইটও গত বিশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। কীভাবে এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে, তাও ভোটারদের কাছে পরিষ্কার নয়। ভোটাররা এ পরিস্থিতির জন্য ডেমোক্র্যাটদের ওপর দোষারোপ করছে। যদিও এ পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার কোনো পরিকল্পনা রিপাবলিকানরাও দিতে পারছে না। তাই প্রতিদিন নিজের পকেট থেকে বাড়তি ডলার হারানোর কষ্ট ভোটারদের বাইডেন প্রশাসনের নীতির বিপক্ষে ভোট দিতে উৎসাহিত করেছে। অনেক ডেমোক্র্যাট সমর্থকও মূল্যস্ফীতির কারণে রিপাবলিকানদের ভোট দিয়েছেন।
অন্যদিকে কিছু দিন আগে গর্ভপাত নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের একটি রায়ের ফলে জনগণ নড়েচড়ে উঠেছে। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে গর্ভপাত একটি অমীমাংসিত ইস্যু। রিপাবলিকানরা চায় গর্ভপাত নিষিদ্ধ হোক। গর্ভপাতকে তারা শিশু হত্যা হিসাবে প্রচার করে। কোনো অবস্থাতেই তারা গর্ভপাতের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে চায় না।
আবার ডেমোক্র্যাটরা এ বিষয়ে খুবই উদার। তাদের কথা হচ্ছে, শরীর যার সিদ্ধান্ত তার। একজন মহিলা গর্ভধারণ করবে নাকি গর্ভপাত করবে, এটা একান্তই তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। আইন এখানে ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কারণ একজন মহিলার কাজের পরিবেশ, স্বাস্থ্যগত অবস্থা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে তার সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয়টি। তাই একজন মহিলাকে কোনোভাবেই গর্ভপাত নিষিদ্ধ করে সন্তান নিতে বাধ্য করা উচিত নয় বলেই ডেমোক্র্যাটরা মনে করে। রিপাবলিকান প্রভাবিত আদালত যখন গর্ভপাত নিষিদ্ধের বিষয়টি নীতিগতভাবে সমর্থন করে, তখন নারী ভোটাররা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আদালত অবশ্য বলে দিয়েছিল, কোনো রাজ্য চাইলে গর্ভপাতের অধিকার রাখতে পারে।
বুথফেরত ভোটারদের মধ্যে একটি জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৩২ শতাংশ ভোটার মূল্যস্ফীতিকে প্রধান ইস্যু মনে করেন। অন্যদিকে প্রায় ২৭ শতাংশ ভোটার গর্ভপাতের অধিকারকে প্রধান ইস্যু মনে করেন। অবশ্য পেনসিলভানিয়া ও মিশিগানের ভোটারদের কাছে মূল্যস্ফীতির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসাবে উঠে আসে গর্ভপাতের বিষয়টি। নির্বাচনের ফলাফলে এ দুটি রাজ্যে এর প্রতিফলনও দেখা গেছে। পেনসিলভানিয়ায় রিপাবলিকানরা তাদের একটি সিনেট আসন ডেমোক্র্যাটদের কাছে হারায়। মিশিগানেও গভর্নর আবার নির্বাচিত হন, একই সঙ্গে রাজ্য প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের দখলও ডেমোক্র্যাটরা নিয়ে নেয়। মূল্যস্ফীতির কারণে যে বড় পরাজয় হওয়ার কথা ছিল, ডেমোক্র্যাটদের তা আটকে দেয় গর্ভপাতের ইস্যুটি। আমেরিকানদের কাছে এবারের নির্বাচনটি ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকানদের মধ্যে না হয়ে যেন হয়ে ওঠে ‘ইনফ্ল্যাশন বনাম এবরশন’র নির্বাচন।
যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি চার বছর পরপর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হলেও কংগ্রেস নির্বাচন হয় প্রতি দুবছর পরপর। সিনেটররা নির্বাচিত হন ছয় বছরের জন্য। এ জন্য ১০০ আসনের সিনেটের এক-তৃতীয়াংশে ভোট হয় প্রতি দুই বছর পরপর। আবার কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হন ২ বছরের জন্য। তাই কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি আসনে ভোট হয় প্রতি দুবছর পরপর। মজার বিষয় হচ্ছে, ১৯৩৮ সাল থেকে দুটি ব্যতিক্রম ছাড়া মধ্যবর্তী নির্বাচনে সবসময়ই ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের দল আসন হারিয়েছে।
১৯৩৮ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সবচেয়ে বেশিসংখ্যক ৭৭টি আসন হারান মধ্যবর্তী নির্বাচনে। ২০১৮ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সিনেটে দুটি আসন পেলেও প্রতিনিধি পরিষদে ৪১টি আসন হারান। এ ছাড়া বারাক ওবামা ২০১০ সালে উভয়কক্ষে হারান ৬৯টি আসন এবং ২০১৪ সালে হারান ২১টি আসন। এ বিবেচনায় প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যবর্তী নির্বাচনে হারানো আসনের বিপরীতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অনেক কম আসন হারাচ্ছেন।
অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময় যে দুটি মধ্যবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের আসন সংখ্যা বেড়েছিল, তার একটি ঘটেছিল ২০০২ সালে। রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার বুশের সময়ে এ নির্বাচন হয় নাইন-ইলেভেনের টুইন টাওয়ার হামলার পরপর। বিশ্লেষকদের ধারণা, আমেরিকার জনগণ তখন দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ ছিল। তাই প্রেসিডেন্টের হাতকে শক্তিশালী করে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ম্যান্ডেট দেয়।
কিন্তু কোনো বিশ্লেষণ কাজ করেনি প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বেলায়। বিল ক্লিনটন ১৯৯৪ সালে তার প্রথম মধ্যবর্তী নির্বাচনে ৬০টি আসন হারালেও দ্বিতীয় মেয়াদে যখন মনিকা লিউনস্কি স্ক্যান্ডালে নাজেহাল, তখন ১৯৯৮ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে পাঁচটি আসনে বেশি বিজয়ী হন!
এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বড় ধরনের কোনো প্রভাব ফেলবে বলে মনে হয় না। বৈদেশিক নীতিতে ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকানদের মধ্যে কেউ একটু বেশি সরব, কেউ তুলনামূলক কম সরব থাকে। নীতি অনেকটা একইরকম থাকে। বাংলাদেশে যারা অপেক্ষা করছেন ‘স্যাংশন’ বিষয়ে কোনো পরিবর্তন আসে কিনা নির্বাচনের পর-তারাও কোনো পরিবর্তন দেখবেন বলে মনে হয় না। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষায় বাংলাদেশের অবস্থান এবং অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পরিস্থিতিই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে।
বর্তমান স্যাংশনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আমলে, ২০১৮ সালের পর থেকে। তাই যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট পরিবর্তনে কিংবা প্রতিনিধি পরিষদে জয়-পরাজয়ে বাংলাদেশের ব্যাপারে বড় কোনো পরিবর্তন হবে না, যদি না বৈশ্বিক রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় ভিন্ন কোনো কারণে।
যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিকরা এখন ধীরে ধীরে কাজ শুরু করবেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে।