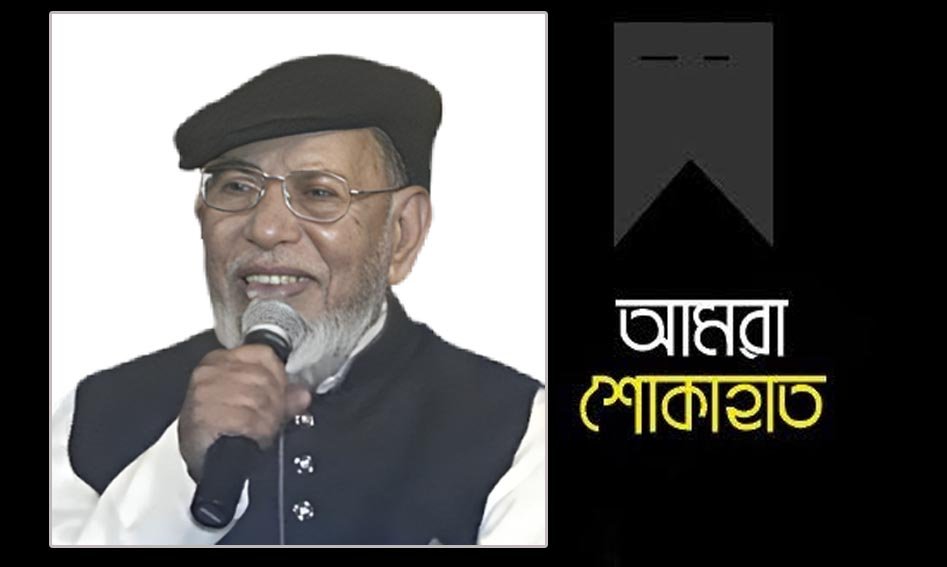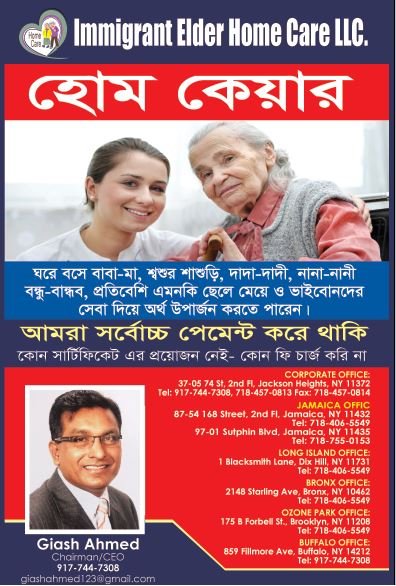রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় সেল্ফ সেন্সরশিপ !

- প্রকাশের সময় : ০৫:৫৩:২৯ অপরাহ্ন, শুক্রবার, ২৩ নভেম্বর ২০১৮
- / ৮০৩ বার পঠিত
গোলাম সারওয়ার: বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার অবারিত উচ্চ শিক্ষায়তন। মুক্তচিন্তা একটি বিশেষায়িত চিন্তন প্রক্রিয়া, যেখানে কোনোরকম সীমাবদ্ধতা কিংবা প্রতিবন্ধকতার প্রভাব থাকে না। সামগ্রিকভাবে যুক্তির্পূণ ও প্রগতিশীল সচেতন চিন্তার প্রতিফলন বা প্রয়োগকেই মুক্তচিন্তার সংজ্ঞা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় চিন্তার উন্মুক্ততার স্থান। এখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মুক্তমনা হিসেবে গড়ার সুযোগ পায়। মুক্তবিশ্বাস এবং মতবাদকে স্ব স্ব স্থানে মর্যাদা ও সন্মানের মাধ্যমে নিজের প্রগতিশীলতা, মননশীলতাকে ধারণ ও লালন করার উপযুক্ত ক্ষেত্রই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাধীনভাবে নিজের মতামত প্রকাশের অধিকারের স্ফূরণ ঘটে এখানে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে মূলত এর চিন্তা ও মতামতের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের উপর। বিশ্ববিদ্যালয় একটি সার্বজনীন এবং সর্বপ্রকার সংকীর্ণতামুক্ত সামাজিক শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। গণতন্ত্রের ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস, প্রগতির ইতিহাস, মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার ইতিহাস আসলে বিশ্ববিদ্যালয়েরই ইতিহাস। অথচ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক চর্চার অনুষঙ্গ মুক্ত সাংবাদিকতা অনেকটা অন্তরীণ। ‘সেল্ফ সেন্সরশিপের’ জালে বন্দি হয়ে পড়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকরা। এই ‘সেল্ফ সেন্সরশিপের’ কারণে এখানকার সাংবাদিকরা তাঁদের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকে সরে যাচ্ছেন। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পক্ষই দায়ি হোক না কেন, তা জাতির জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কারণ, এই বিশ্ববিদ্যালয় যারা পরিচালনা করেন, তাঁরা সবাই উঁচুমানের মানুষ। উচ্চ শিক্ষিত, উচ্চ ডিগ্রিধারি। তাঁরা জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, গবেষক। তাঁদেরই গণতন্ত্রমনা হওয়া একান্ত উচিত। তারপরেও তাঁদের অনেকে নেতিবাচক ধ্যান-ধারণা নিয়ে মত্ত! দেশ ও জাতির কল্যাণকামী তাদেরইতো হবার কথা! কিন্তু আমরা একি দেখছি! শিক্ষার সুফল আমরা কোথায় গেলে পাবো? বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি মুক্ত সাংবাদিকতার চর্চা না হয়, সন্মানিত শিক্ষকদের অশিক্ষকসূলভ মনোভাবের কারণে শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে যদি সম্ভাবনাময় সাংবাদিকরা ‘সেল্ফ সেন্সরশিপ’ অর্থাৎ স্বপ্রণোদিত বর্জনের আশ্রয় নেয়, তবে তারা শৃঙ্খলিতভাবে গড়ে উঠবে। পালকহীন পাখির মতো শুধু ডানা ঝাপটাবে। উন্মুক্ত আকাশে ওড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। তারা নির্র্দিষ্ট গ-ির মধ্যে থাকাটাকেই নিরাপদ বলে মনে করবে। এটা জাতির জন্য অকল্যাণকর।
বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যারা নিয়োগ পান, তাঁরা সবাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী। এখানকার শিক্ষার্থী হওয়ার ফলেই তাঁরা মুক্ত সাংবাদিকতা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হন। রাষ্ট্রযন্ত্রের কারণে, সন্ত্রাসীদের ভয়ে কিংবা জঙ্গি আতঙ্কে নয়। তাঁদের শিক্ষাজীবন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় তাঁরা শিক্ষকদের অনিয়মের ‘ডেপথ নিউজ’ করা থেকে বিরত থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কিংবা কোনো শিক্ষকের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের অভিযোগের নিউজ করতে তাঁরা ভয় পান। কারণ, শিক্ষকদের হাতে তাঁদের প্রাণ। শিক্ষকদের মনোভাবের ওপর রেজাল্টের অনেক কিছু র্নিভর করে। কোনো শিক্ষার্থী যদি শিক্ষকের রোষানলে পড়েন, তবে তাঁর শিক্ষাজীবন বিপন্ন হওয়ার সমূহ আশঙ্কা দেখা দেয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের নজির আছে। যার কারণে স্বপ্রণোদিত হয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকরা সেন্সরশিপের আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। এখানকার বিভিন্ন বিভাগে পড়ুয়া সাংবাদিকদের নিজের বিভাগের কোনো কোনো শিক্ষক দিনের পর দিন ক্লাসে আসেন না, আসলেও ঠিকমতো পড়ান না; কেউ কেউ দু’চারটি ক্লাস নিয়ে পরীক্ষার আগে তড়িঘড়ি করে কোর্স শেষ করে দেন। অর্থের প্রতি আসক্তি হয়ে নিজের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা না ভেবে এখান থেকে ছুটি নিয়ে বছরের পর বছর কোনো কোনো শিক্ষক অন্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেন। এ ধরনের পঠন-পাঠন সংশ্লিষ্ট অনেক কাজে কিছু কিছু শিক্ষক তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে চরম গাফিলতি করেন। তাতে করে শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষতির সম্মুখিন হন। তাঁদের শিক্ষাজীবনে ঘাটতি থেকে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে কি দুর্নীতি হয়না, এখানে কি শিক্ষকরা অনৈতিক কাজ করেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে নৈতিক স্খলনজনিত অভিযোগ থাকে না ! শিক্ষকরা অনেকে অশুদ্ধাচার কাজ করে থাকেন। যেমন, গবেষণার কাজে দুর্নীতি, মাদক সেবন, এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে আরেক শিক্ষকের জঘন্য কথাবার্তা বলা; রাজনীতিতে একই দলভুক্ত শিক্ষকদের স্বার্থের কারণে বিভক্তি- এই ধরনের নানা নেতিবাচক কর্মকা- হচ্ছে। এরপরেও কেনো এখানকার সাংবাদিকরা সে সবের অনুসন্ধানমূলক নিউজ করেন না! কেনো তাঁরা ঝুঁকি নিতে চান না। প্রচ- ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় তারা এসবের বিরুদ্ধে নিউজ করেন না। কেবলমাত্র সিন্ডিকেট কর্তৃক শিক্ষকদের কোনো ঘটনার সিদ্ধান্ত হলেই তারা গা বাঁচানোর নিউজ করে থাকেন। আমার জানা মতে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাডেমিক সংক্রান্ত কোনো অনুসন্ধানমূলক নিউজ আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। তাঁরা এসব দেখেও না দেখার ভান করেন, শুনেও না শোনার ভান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দু’চারটি নেতিবাচক নিউজ হলেও সেগুলো শহরের সাংবাদিকরা করেন। এইভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শৃঙ্খলিত হয়ে পড়েছে। মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা কেন্দ্রে মুক্ত সাংবাদিকতা আজ অন্তরীণ। ‘সেল্ফ সেন্সরশিপের’ বেড়াজালে আটকা পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া সাংবাদিকরা। যার কারণে এখানকার সাংবাদিকরা নির্জিব, নির্লিপ্ত। স্পন্দনহীন হয়ে পড়েছে মতিহার ক্যাম্পাসের সাংবাদিকতা।
 বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা প্রকৃতপক্ষেই ক্যাম্পাসকে মুক্ত সাংবাদিকতার চর্চা কেন্দ্র হিসেবে দেখতে চায়। সেজন্য সর্বাগ্রে শিক্ষকদের হতে হবে গণতন্ত্রমনা, মুক্তমনা। শিক্ষার্থীদের গণতন্ত্রমনা হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকের আচরণ গুরুত্বর্পূণ ভূমিকা পালন করে। একজন শিক্ষকের গণতান্ত্রিক আচরণ, শিক্ষকসূলভ মনোভাব, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, অধ্যাবসায়, আন্তরিকতা ,গবেষণামুখিনতা, সততা এবং ব্যক্তি হিসেবে নমনীয়তা শিক্ষার্থীর জন্য আশীর্বাদ। এর বিপরীতে শিক্ষকের অগণতান্ত্রিক আচরণ, আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা, খামখেয়ালিপনা, ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা, অসততা, অহমিকা, সত্য প্রকাশে বাধা দেওয়া প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের জন্য অভিশাপ। শিক্ষক হবেন সামাজিক মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। দৃষ্টিভঙ্গিতে নৈর্ব্যক্তিক ও প্রসারিত, স্বপ্নে উদার এবং সঞ্চারি, প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় এবং উন্নত, কর্মে দক্ষ, গবেষক এবং সাধক। সর্বোপরি বৃহৎ মানবসমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা। একজন শিক্ষকের মধ্যে এসব গুণাবলির সমন্বয় ঘটলে তিনি শিক্ষার্থীর হৃদয় ও চিন্তায় দীর্ঘকালীন ছাপ রাখতে পারেন। এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে মুক্তচিন্তা ও মুক্তিবুদ্ধির চর্চার কেন্দ্র। কোনও সভ্য সমাজের অন্যতম অধিকার হলো, বাক স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। সত্য বলার অধিকার যে প্রতিষ্ঠান বা সমাজ নিশ্চিত করতে না পারে, সে প্রতিষ্ঠানে বা সমাজে গণতন্ত্র আছে এমনটি মনে করার কোনও কারণ নেই। জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় বলা হয়েছে, ‘প্রত্যেকটি মানুষের স্বাধীনভাবে তথ্য ও মতামত প্রকাশের অধিকার আছে। সংবাদপত্রের দায়িত্ব হলো তথ্য সংগ্রহ করা এবং জনগণের কাছে তা পরিবেশন করা’। বাংলাদেশের সংবিধানের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অধ্যায়ে (অনুচ্ছেদ ৩.৯) উল্লেখ আছে,“(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল”। সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা বলতে আমরা বুঝি, লিখবার এবং তা প্রকাশ করার স্বাধীনতা। ১৮৯৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সিডিশন বিল আইনে পরিণত হওয়ার আগের দিে কোলকাতা টাউন হলে এক জনসভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘কণ্ঠরোধ’ পড়ে বলেন, “সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না।’’ বলা বাহুল্য, যে কোনো সমাজের জন্য আত্মগোপন নয়, আত্মপ্রকাশই শ্রেয়। আর সেই প্রকাশ হতে হবে সত্যনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর। মত বা ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে সেই সপ্তদশ শতকে ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন ইংরেজ কবি মিল্টন। তাঁর লেখা অ্যারিওপ্যাজিটিকায় তিনি এইভাবে বলেছেন, “দাও আমায় জ্ঞানের স্বাধীনতা দাও, কথা বলার স্বাধীনতা দাও, মুক্তভাবে বিতর্ক করার স্বাধীনতা দাও”। এসব সুন্দর সুন্দর কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রিধারী শিক্ষকরা সবই জানেন, তারপরেও কেনো তারা সত্য কথা বললে রুষ্ট হবেন! কেনো তারা ছাত্র সাংবাদিকদের সত্য প্রকাশে সাহস না জুগিয়ে অশিক্ষকসূলভ আচরণ দ্বারা তাদের শিক্ষাজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সচেষ্ট হবেন ! বিখ্যাত রাজনৈতিক দার্শনিক ভলতেয়ার বলেছেন, “আমি তোমার প্রতিটি কথার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি, কিন্তু আমৃত্যু স্বীকার করে যাবো তোমার বলার স্বাধীনতা আছে”।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা প্রকৃতপক্ষেই ক্যাম্পাসকে মুক্ত সাংবাদিকতার চর্চা কেন্দ্র হিসেবে দেখতে চায়। সেজন্য সর্বাগ্রে শিক্ষকদের হতে হবে গণতন্ত্রমনা, মুক্তমনা। শিক্ষার্থীদের গণতন্ত্রমনা হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকের আচরণ গুরুত্বর্পূণ ভূমিকা পালন করে। একজন শিক্ষকের গণতান্ত্রিক আচরণ, শিক্ষকসূলভ মনোভাব, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, অধ্যাবসায়, আন্তরিকতা ,গবেষণামুখিনতা, সততা এবং ব্যক্তি হিসেবে নমনীয়তা শিক্ষার্থীর জন্য আশীর্বাদ। এর বিপরীতে শিক্ষকের অগণতান্ত্রিক আচরণ, আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা, খামখেয়ালিপনা, ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা, অসততা, অহমিকা, সত্য প্রকাশে বাধা দেওয়া প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের জন্য অভিশাপ। শিক্ষক হবেন সামাজিক মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। দৃষ্টিভঙ্গিতে নৈর্ব্যক্তিক ও প্রসারিত, স্বপ্নে উদার এবং সঞ্চারি, প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় এবং উন্নত, কর্মে দক্ষ, গবেষক এবং সাধক। সর্বোপরি বৃহৎ মানবসমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা। একজন শিক্ষকের মধ্যে এসব গুণাবলির সমন্বয় ঘটলে তিনি শিক্ষার্থীর হৃদয় ও চিন্তায় দীর্ঘকালীন ছাপ রাখতে পারেন। এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে মুক্তচিন্তা ও মুক্তিবুদ্ধির চর্চার কেন্দ্র। কোনও সভ্য সমাজের অন্যতম অধিকার হলো, বাক স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। সত্য বলার অধিকার যে প্রতিষ্ঠান বা সমাজ নিশ্চিত করতে না পারে, সে প্রতিষ্ঠানে বা সমাজে গণতন্ত্র আছে এমনটি মনে করার কোনও কারণ নেই। জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় বলা হয়েছে, ‘প্রত্যেকটি মানুষের স্বাধীনভাবে তথ্য ও মতামত প্রকাশের অধিকার আছে। সংবাদপত্রের দায়িত্ব হলো তথ্য সংগ্রহ করা এবং জনগণের কাছে তা পরিবেশন করা’। বাংলাদেশের সংবিধানের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অধ্যায়ে (অনুচ্ছেদ ৩.৯) উল্লেখ আছে,“(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল”। সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা বলতে আমরা বুঝি, লিখবার এবং তা প্রকাশ করার স্বাধীনতা। ১৮৯৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সিডিশন বিল আইনে পরিণত হওয়ার আগের দিে কোলকাতা টাউন হলে এক জনসভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘কণ্ঠরোধ’ পড়ে বলেন, “সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না।’’ বলা বাহুল্য, যে কোনো সমাজের জন্য আত্মগোপন নয়, আত্মপ্রকাশই শ্রেয়। আর সেই প্রকাশ হতে হবে সত্যনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর। মত বা ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে সেই সপ্তদশ শতকে ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন ইংরেজ কবি মিল্টন। তাঁর লেখা অ্যারিওপ্যাজিটিকায় তিনি এইভাবে বলেছেন, “দাও আমায় জ্ঞানের স্বাধীনতা দাও, কথা বলার স্বাধীনতা দাও, মুক্তভাবে বিতর্ক করার স্বাধীনতা দাও”। এসব সুন্দর সুন্দর কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রিধারী শিক্ষকরা সবই জানেন, তারপরেও কেনো তারা সত্য কথা বললে রুষ্ট হবেন! কেনো তারা ছাত্র সাংবাদিকদের সত্য প্রকাশে সাহস না জুগিয়ে অশিক্ষকসূলভ আচরণ দ্বারা তাদের শিক্ষাজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সচেষ্ট হবেন ! বিখ্যাত রাজনৈতিক দার্শনিক ভলতেয়ার বলেছেন, “আমি তোমার প্রতিটি কথার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি, কিন্তু আমৃত্যু স্বীকার করে যাবো তোমার বলার স্বাধীনতা আছে”।
 বাংলাদেশে মুক্ত সাংবাদিকতার প্রধান অন্তরায় রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চর্চা না থাকা। সামাজিক সংস্থাগুলোর অনেক ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। বিশেষ করে মুক্ত সাংবাদিকতার যেখানে চর্চা হওয়া অপরিহার্য, সেই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও গণতন্ত্র এখন অনুপস্থিত। ভিসি নিয়োগ, শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে ছাত্র সংসদ নির্বাচনসহ অনেক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ধারা মানা হচ্ছে না। যেখানে গণতান্ত্রিক আচরণ রপ্ত করার জায়গা, সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই যদি অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ হয়; তবে সেখান থেকে মুক্ত সাংবাদিকতা আশা করা বাতুলতা মাত্র। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক অর্থাৎ নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকরা শিক্ষকদের সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করলে তাদের শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এই আশঙ্কা থাকলে তিনিতো তথ্য প্রকাশে বিরত থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। তাঁদের শিক্ষাজীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁরা ‘সেল্ফ সেন্সরশিপে’ যেতে বাধ্য হচ্ছেন। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে দেশ ও জাতির উপর। মুক্ত, সাহসী, সৎ ও মানসম্মত সাংবাদিকতা আশা করতে হলে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মুক্ত সাংবাদিকতার চর্চা করার পরিবেশ করে দিতে হবে কর্তৃপক্ষকে। সাংবাদিকতা ক্রমাগত অনুশীলনে হয়ে ওঠা একটি প্রফেশন। এজন্য সাংবাদিকতার মতো মহান এবং প্রথম শ্রেণির পেশায় যারা আসতে আগ্রহী তাদেরকে ছাত্রজীবন থেকেই অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। ছাত্রজীবনই সাংবাদিকতা শুরুর উপযুক্ত সময়। এদেশে সাংবাদিকদের প্রায় শতভাগ ছাত্রজীবন থেকেই সাংবাদিকতা পাঠ শুরু করেন। ফলে ছাত্রজীবন শেষ করে সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্বেই প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাটুকু অর্জিত হয়। আমার মনে হয়, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ এখানে বড় ভূমিকা নিতে পারে। জানা মতে,১৯৯১ সালে ফিলিপাইন ‘ক্যাম্পাস জার্নালিজম অ্যাক্ট অব ১৯৯১’ নামে একটি আইন প্রণয়ন করে। ওই আইনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাংবাদিকতার একটি গাইডলাইন নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যেখানে মুক্ত সাংবাদিকতার স্বার্থে রাষ্ট্রীয় টাকায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সেখানকার তরুণ ও উদীয়মান সাংবাদিকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ, কর্মশালার আয়োজন করার কথা বলা হয়েছে। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। মুক্ত সাংবাদিকতার অপর নাম দায়িত্বশীলতা। মুক্ত সাংবাদিকতা মানে এই নয় যে, তিনি তার ইচ্ছে মতো যা কিছু লিখবেন, যাকে খুশি আক্রমণ করবেন, যাকে খুশি অতি তোষণ করবেন। এক্ষেত্রে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় মুক্ত সাংবাদিকতার জন্য যথার্থ কর্মশালা, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পাশাপাশি সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের স্বার্থে ক্যাম্পাসের সাংবাদিকদের শিক্ষাজীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। এর ফলে মুক্ত সাংবাদিকতার অন্যতম বাধা ‘সেল্ফ সেন্সরশিপের’ চিন্তা-ভাবনা থেকে সরে আসতে পারবেন ক্যাম্পাসের সাংবাদিকরা। ফলশ্রুতিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্ত সাংবাদিকতার পরিবেশ ফিরে আসবে।
বাংলাদেশে মুক্ত সাংবাদিকতার প্রধান অন্তরায় রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চর্চা না থাকা। সামাজিক সংস্থাগুলোর অনেক ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। বিশেষ করে মুক্ত সাংবাদিকতার যেখানে চর্চা হওয়া অপরিহার্য, সেই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও গণতন্ত্র এখন অনুপস্থিত। ভিসি নিয়োগ, শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে ছাত্র সংসদ নির্বাচনসহ অনেক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ধারা মানা হচ্ছে না। যেখানে গণতান্ত্রিক আচরণ রপ্ত করার জায়গা, সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই যদি অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ হয়; তবে সেখান থেকে মুক্ত সাংবাদিকতা আশা করা বাতুলতা মাত্র। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক অর্থাৎ নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকরা শিক্ষকদের সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করলে তাদের শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এই আশঙ্কা থাকলে তিনিতো তথ্য প্রকাশে বিরত থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। তাঁদের শিক্ষাজীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁরা ‘সেল্ফ সেন্সরশিপে’ যেতে বাধ্য হচ্ছেন। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে দেশ ও জাতির উপর। মুক্ত, সাহসী, সৎ ও মানসম্মত সাংবাদিকতা আশা করতে হলে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মুক্ত সাংবাদিকতার চর্চা করার পরিবেশ করে দিতে হবে কর্তৃপক্ষকে। সাংবাদিকতা ক্রমাগত অনুশীলনে হয়ে ওঠা একটি প্রফেশন। এজন্য সাংবাদিকতার মতো মহান এবং প্রথম শ্রেণির পেশায় যারা আসতে আগ্রহী তাদেরকে ছাত্রজীবন থেকেই অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। ছাত্রজীবনই সাংবাদিকতা শুরুর উপযুক্ত সময়। এদেশে সাংবাদিকদের প্রায় শতভাগ ছাত্রজীবন থেকেই সাংবাদিকতা পাঠ শুরু করেন। ফলে ছাত্রজীবন শেষ করে সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্বেই প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাটুকু অর্জিত হয়। আমার মনে হয়, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ এখানে বড় ভূমিকা নিতে পারে। জানা মতে,১৯৯১ সালে ফিলিপাইন ‘ক্যাম্পাস জার্নালিজম অ্যাক্ট অব ১৯৯১’ নামে একটি আইন প্রণয়ন করে। ওই আইনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাংবাদিকতার একটি গাইডলাইন নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যেখানে মুক্ত সাংবাদিকতার স্বার্থে রাষ্ট্রীয় টাকায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সেখানকার তরুণ ও উদীয়মান সাংবাদিকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ, কর্মশালার আয়োজন করার কথা বলা হয়েছে। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। মুক্ত সাংবাদিকতার অপর নাম দায়িত্বশীলতা। মুক্ত সাংবাদিকতা মানে এই নয় যে, তিনি তার ইচ্ছে মতো যা কিছু লিখবেন, যাকে খুশি আক্রমণ করবেন, যাকে খুশি অতি তোষণ করবেন। এক্ষেত্রে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় মুক্ত সাংবাদিকতার জন্য যথার্থ কর্মশালা, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পাশাপাশি সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের স্বার্থে ক্যাম্পাসের সাংবাদিকদের শিক্ষাজীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। এর ফলে মুক্ত সাংবাদিকতার অন্যতম বাধা ‘সেল্ফ সেন্সরশিপের’ চিন্তা-ভাবনা থেকে সরে আসতে পারবেন ক্যাম্পাসের সাংবাদিকরা। ফলশ্রুতিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্ত সাংবাদিকতার পরিবেশ ফিরে আসবে।
লেখক: ডেপুটি রেজিস্ট্রার,রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক সভাপতি, রাজশাহী প্রেসক্লাব । e-mail: gsarwarjru983@gmail.com