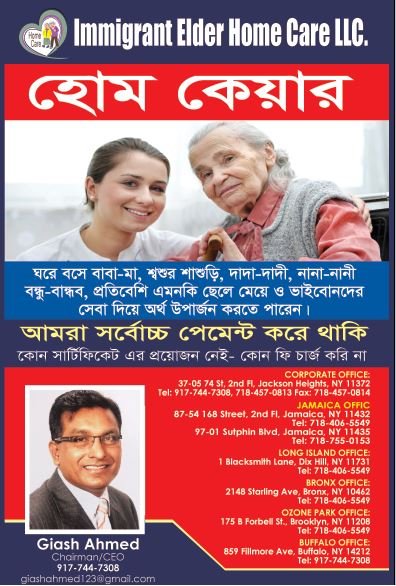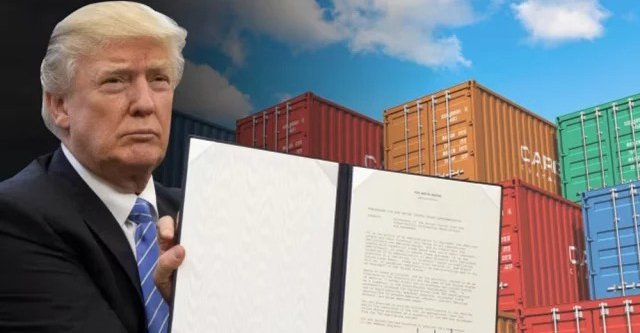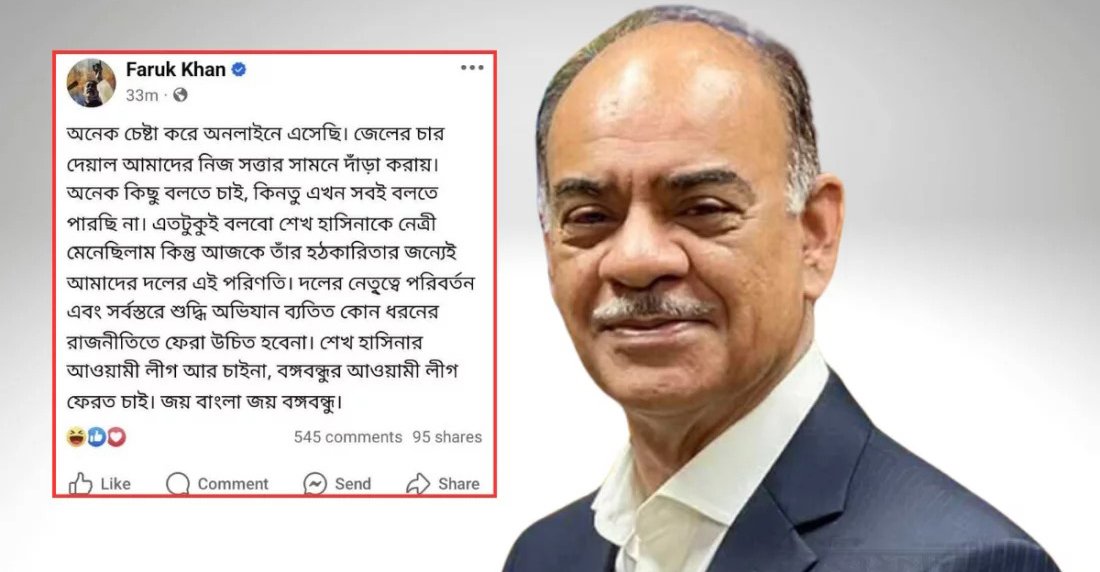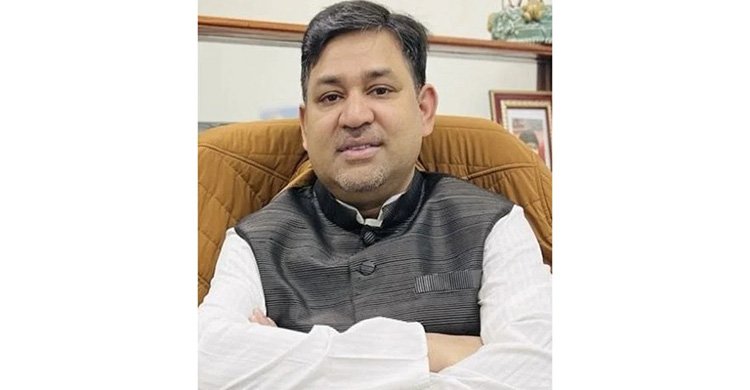প্রণব মূখার্জীর দেয়াল পাড়ি

- প্রকাশের সময় : ০৯:১৯:০৭ অপরাহ্ন, শুক্রবার, ২২ জুন ২০১৮
- / ৫৯০ বার পঠিত
আবু জাফর মাহমুদ: ভারতে সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনীতি ও প্রশাসনের ধারালো হাতিয়ারে চলছে ব্যবহার। উপমহাদেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ভেঙ্গে সমৃদ্ধির তূলনায় আতœহননের চলছে নারকীয় উৎসব। এসময় জ্ঞান ও শিক্ষা রাজনীতির অশ্লীল প্রতিযোগীতার লাগাম কতটুকু টেনে রাখতে পারছে, তার সামান্য চেষ্টা আসছে নজরে। আমরা যেনো জানার দৃষ্টিতেই করি দৃষ্টিপাত।
সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সমগ্র রাজনৈতিক অঙ্গন এবং সমাজ জীবনে অস্থিরতা ছড়িয়ে চলেছে। এই অস্থিরতা হিন্দু প্রভাবিত ভারতীয় সমাজের ভেতরের জাত-গোষ্ঠী বিভেদে উত্তাপের আগুণ বিস্তৃত করছে। প্রশাসন, পুলিশ, প্রতিরক্ষা বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা ও বিচার বিভাগ সহ সরকার এবং রাষ্ট্রপরিচালনায় কর্তৃত্ব করছে কথিত উচ্চজাত বা সুবিধাভোগী এবং বিদ্বেষী জাতের সম্প্রদায়। ভারতব্যাপী তাই চলছে প্রতিবাদ।
সংখ্যালঘু চতুর ও হিংস্যুটে গোষ্ঠীটি ভারত দখলে নিয়েছে ১৯৪৭ সনে ভারত দখলে নেয়ার শুরুতেই। কিভাবে তা সম্ভব হলো? বৃটিশ দখলদারিত্বের কালে স্থানীয় বৃটিশ প্রশাসনে হিন্দু মুসলিম শিখ সহ সকল জাতিগোষ্ঠী থেকে প্রতিরক্ষাবাহিনী, পুলিশ ও বেসামরিক প্রশাসনে নিয়োগে সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী থেকে লোক বাছাই করা হতো। শিক্ষার সুযোগও ছিলো তাদের জন্যে। বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হবার কালে এবং ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন চালু হবার প্রেক্ষিতে বৃটেনের ভারত ছাড়ার পরিস্থিতি অনিবার্য্য হয়ে গেলে অনুগত অপদার্থদের কাছে টানার যুক্তি দেখা দেয়।
কংগ্রেস-মুসলিম লীগ কম্যুনিষ্ট পার্টিসহ প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল বা সমাজের প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে সমঝোতার প্রয়োজন হয়ে যায়। হিন্দু-মুসলমান নেতাদের মধ্যে ভারতীয় জাতিয়তাবাদী দেশপ্রেম প্রধান্যে থাকার চেয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাভোগের জন্যে কৌশল নিয়ে বিভেদ হয়ে যায়। ফলে ভারতীয় একতার চেয়ে বিভেদ বিভক্তির ভিত্তির গুরুত্ব এই শিক্ষিত ও বৃটিশ লেজুড়দের মধ্যে প্রাধান্য পায়।
অশিক্ষিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে যে যেভাবে পেরেছেন প্রভাবিত ও পক্ষে-বিপক্ষে ঠেলে দেন এবং বৃটিশ প্রশাসন তাদের প্রজা ও দাসদের পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক রক্তপাত এবং ভিটেবাস্তুচ্যুত হবার নির্মমতাকে রসিকতার সাথে উপভোগ করেন। ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হলো গড়া হলো ভারত এবং পাকিস্তান। বৃটিশ প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় চালু হয়ে এই দুটি রাষ্ট্র নিজেদের অসঙ্গতিগুলো নিয়েই বেড়ে উঠতে থাকে।
ভারত বিভক্তির আগে যেসকল রাজনৈতিক দল আতœপ্রকাশ হয়েছিলো তার কিছুটা ধারণা দরকার। বিজেপির বর্তমান রাজনৈতিক ও নীতিগত কর্মকান্ড নিয়ে ভারতীয়দের ভেতর এবং বাংলাদেশে যথেষ্ট বিরক্তি দেখা দেয়া এবং নীচ প্রকৃতির মানসিকতার রাজনৈতিক শক্তিগুলো সাধারণ নাগরিকদেরকে বিভ্রান্ত করার ঝোঁক অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় এই তথ্য সামনে আনা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করা হচ্ছে।
ইন্ডিয়ান ন্যাশান্যাল কংগ্রেস (১৮৮৫), শিরমণি আকালি দল (১৯২০) রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (১৯২৫), কম্যুনিষ্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (১৯২৫), অল ইন্ডিয়া মজলিশ-ই-ইত্তেহাদুল মুসলেমিন (১৯২৭), আহরার পার্টি (১৯২৯), মজলিশ আহরার-উল-ইসলাম (১৯২৯), রেভ্যুলুশানেরী কম্যুনিষ্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (১৯৩৪), দ্রাবিদাড় কাজগাম (১৯৩৮), জম্মু এন্ড কাস্মীর ন্যাশানেল কনফারেন্স (১৯৩৯), অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক (১৯৩৯), রেভোলুশানেরী সোচিয়ালিষ্ট পার্টি (১৯৪০), অখিল ভারতীয় গোর্খা লীগ (১৯৪৩)।
এই দলগুলো বৃটিশ খেদানোর লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতা করে তৎপর ছিলো বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। এ ছাড়া আরো দল থাকতে পারে যারা নিজেদের অবস্থান থেকে এই সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলো। তবে আন্দোলন ও রাজনীতির বাস্তবতায় এই সব দল পরবর্তীতে বিলুপ্তি ঘোষণা দেয় এবং কোন কোনটা আরো শক্তিশালী হয়। কোন কোনটা আবার নিজেরাই মিলে একমঞ্চ গড়েছে।
ফার্স্ট সেশান অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস (১৮৮৫), ইষ্ট ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন(১৮৬৭), ইন্ডিয়া হাউস (১৯০৫-১৯১০), (১৮৬৭), দ্য ইন্ডিয়ান সোসিয়েলিষ্ট (১৯০৫-১৯১৪), ১৯২০-১৯২২, ঘাডার পার্টি (১৯১৩-১৯১৯), জাষ্টিস পার্টি (১৯২০-১৯৪৪), স্বরাজ পার্টি (১৯২৩-১৯৩৫), অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ (১৯০৬-১৯৪৭), ঘাডার পার্টি মুভমেন্ট, ইউএসএ (১৯১৩-১৯১৯), অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা (১৯১৫), রেডিক্যাল ডেমোকক্র্যাটিক পার্টি (১৯৪০-১৯৪৮), ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি (১৯৪২-১৯৪৫), হিন্দুস্থান সোসিয়েলিষ্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশন (১৯২৮-১৯৩৬), অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ (১৯৪০-১৯৪৭), ইন্ডিজ লেজিওন (১৯৪২-১৯৪৫)। এরকম অনেকগুলো রাজনৈতিক দলের উৎপত্তির খবরাখবর বিভিন্ন দলিলে পায়া যায়। শেষ পর্যন্ত এসকল নেতৃত্ব ভারত বিভক্তি ঠেকাতে পারেননি, যখন ভারতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে নিয়ন্ত্রণ কুক্ষিগত করার বিষয়ে সাম্প্রদায়িক চেতনাকে প্রধান হাতিয়ার করার অনিবার্য্যতা দেখা দেয়। জাত গোষ্ঠীর কর্তৃত্বকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ কৌশল রাজনীতিতে আছেই। বিভিন্ন জাতে বিভক্ত এবং বিভেদ বিদ্বেষে অরাজক রীতিনীতিতে ভরপুর সমাজে কেবলমাত্র ৩% ব্রাম্মণদের একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদ উস্কিয়ে দেয়া ছাড়া আর মোক্ষম কোন কৌশল তৎকালীন বাস্তবতায় কি ছিলো? জওহর লাল নেহেরুকে গান্ধীজী পন্ডিত বলে সম্বোধন করতেন তার জ্ঞানের স্বীকৃত যোগ্যতায়।
বৃটিশ প্রশাসন, প্রতিরক্ষা বাহিনী পুলিশ ও বিচার বিভাগে নিয়োজিত ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে অবিভক্ত ভারত সরকারের রাখার বিষয়ে জিন্নাহ-নেহেরুর আলোচনা ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সে সময় বৃটিশ প্রতিরক্ষা বাহিনীতে হিন্দু-মুসলমান ছিলেন সমান সমান। এ নিয়ে কোন বিতর্ক ছিলোনা। পুলিশে মুসলমান ছিলো ৩৭% এটাকে ৪০% করতে নেহেরুর কাছে অনুরোধ ছিলো জিন্নাহর। এভাবে খুবই ছোটকাটো বিষয়ে তারা ইচ্ছে করলে এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমে এককাট্টা থাকা সম্ভব হলে পরবর্তীতে এই নারকীয়তা এড়িয়ে যাওয়া কঠিন ছিলোনা এই বিজ্ঞ নেতাদের। সেক্ষেত্রে আলাদা হয়ে যাওয়া ছিলো একই সাথে থাকা পরিবারকে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধে জড়ানোর চেয়ে উত্তম। আমরা বর্তমানকাল পর্যন্ত পূর্বপুরুষদের পারস্পরিক অসহ্যের কুফল ভোগ করে চলেছি। যাতে বৃটেনের কোনও অসুবিধা হয়নি।
বর্তমানে পাকিস্তানের পূর্ব অংশ ভারতের কর্তৃত্বে তুলে দেবার রাজনীতিবিদ এবং সেনা কর্মকর্তা সহজে পেয়ে যাওয়ায় বাস্তবতা বদল হয়েছে ভারতীয় রাজনৈতিক বাস্তবতার। এসময় এই নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে সুসংহত করাটাকে দেশপ্রেমের প্রাধান্যে আনার গুরুত্ব বেড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রণব মূখার্জীর সাথী আর এস নেতাদের একই মঞ্চে বক্তৃতা করা নিয়ে অন্যেরা হৈচৈ করলেও সহজেই বাস্তবতা মেনে নিতে আমাদের অসুবিধে হয়নি।
 রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদর দপ্তরে কংগ্রেসের সাবেক প্রভাবশালী নেতা এবং সাম্প্রতিক সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মূখার্জি আতিথিয়তা গ্রহণ করে ভাষণ দিয়েছেন হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সম্মেলনে। ভারতীয় রাজনীতিতে এই ঘটনার অনেক বিশ্লেষণ দেখা যাচ্ছে। আসছে আপত্তি আবার আসছে বিভ্রান্তি। আসছে সমর্থনও। এই সাহসিকতার জন্যে আর এস এস তাকে আরেকবার সরকারের নেতার পদে দেখার আশাও প্রকাশ করেছে। তবে কংগ্রেস নেতা সোনিয়াকে ক্ষুদ্ধ থাকার খবর পাওয়া যাচ্ছে।
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদর দপ্তরে কংগ্রেসের সাবেক প্রভাবশালী নেতা এবং সাম্প্রতিক সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মূখার্জি আতিথিয়তা গ্রহণ করে ভাষণ দিয়েছেন হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সম্মেলনে। ভারতীয় রাজনীতিতে এই ঘটনার অনেক বিশ্লেষণ দেখা যাচ্ছে। আসছে আপত্তি আবার আসছে বিভ্রান্তি। আসছে সমর্থনও। এই সাহসিকতার জন্যে আর এস এস তাকে আরেকবার সরকারের নেতার পদে দেখার আশাও প্রকাশ করেছে। তবে কংগ্রেস নেতা সোনিয়াকে ক্ষুদ্ধ থাকার খবর পাওয়া যাচ্ছে।
ভারতের এই নেতা তার বক্তৃতা শুরু করেছেন জাতি, জাতিয়তা এবং দেশপ্রেমের সংজ্ঞা দিয়ে। ইতিহাসের গোড়ায় বিদেশী পর্যটকদের লিখিত মন্তব্যে ভারতীয় সমাজ শৃংখলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। সূদূর অতীত হতে ভারতীয় রীতিনীতির স্বাতন্ত্রবোধ এবং একতার ধারাবাহিকতার কথা তুলে এনেছেন। ভারতীয় সভ্যতার এই বৈশিষ্ট্যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ধরণ দেখা গেছে ইউরোপীয় রাষ্ট্রস্বত্তার অস্তিত্ব দেখা যাবার ও বহু আগে। বলেছেন হিন্দু মুসলমান শিখ ও অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসীসহ সকল জাত গোষ্ঠীদের একাতœায় মিলনের বাঁধনেই গড়া ভারতীয় জাতীয়তা ও দেশপ্রেম।
প্রণব মূখার্জী নিশ্চয়ই সামান্যহলেও হিন্দুত্ববাদ এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রশ্রয় দিয়ে বক্তৃতা করেননি। তিনি ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোকে নিজেদের ভেতর ধৈর্য্য, সহনশীলতা এবং আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে শান্তিতে সহবস্থানের উপর গুরুত্ব দিয়ে তার নিজের বিশ্বাসের অবস্থান পরিস্কার রেখেছেন। দেশপ্রেম এবং ভারতীয় জাতিয়তাবাদের প্রশ্নে তার আন্তরিকতা-কে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিবেচনায় প্রকাশ করেছেন যথাস্থানে। আর এস এস এতে নিজ অবস্থান পরিবর্তন করছেনা। তিনি নিজেও তা আশা করেননি হয়তোবা। তবে ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল সংস্কৃতি-বহুজনের সংস্কৃতিকে সম্মান করার উদাহরণ হলেন তিনি।
ভারতে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতি বর্তমানে যেভাবে সংঘাতে ডুবেছে তার প্রেক্ষিতে প্রণব মুখার্জীর এই বক্তৃতা আর এস এস অনুষ্ঠানের জন্যেই জরুরী ছিলো। যাতে তাদেরকে যা পড়ানো হয় তার পাশাপাশি এই একতা ও শান্তির রাজনীতিকে তূলনার সুযোগ করে দেয়া যায়।
পুঁজির ম্যাজিক আগামীতে ভারতকে কোথায় ঠেলে নেবে? দেশপ্রেমের দিকে নাকি সাম্রাজ্যবাদী পদলেহনে আরো অনুগত হবে? টানাটানিতে যে ধারা জিতবে ওদিকেই কি রাজনৈতিক শক্তির মনোযোগ? নাকি সংঘাতের ঘুর্ণিঝড়ে ভারতকে বিলিয়ে দিয়ে নিজেরাই আখের গুণবেন, তা দেখার জন্যে শিক্ষা ও জ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ জরুরী। ভারতীয় আঞ্চলিক রাজনৈতিক ধারার উপর পরবর্তী লেখার চেষ্টা থাকবে।
(লেখক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাযোদ্ধা)।